রাষ্ট্রভাষা ও স্বাধীনতা আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা
- Update Time : মঙ্গলবার, ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
- ১৬০ Time View

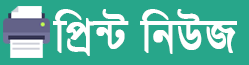
 বুদ্ধিজীবীদের যে অংশ জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরকারের তাঁবেদার হিসেবে কাজ করেছে, তাদের প্রতি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা মানুষকে বিক্ষুব্ধ করেছে। ১৯৬৮ সালে অগ্রগতির ১০ বছরের গুণকীর্তন করে যখন প্রায় প্রতিদিন সংবাদপত্রে একটি করে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছিল, যখন প্রতিদিন মস্ত মস্ত ছবি ছাপা হচ্ছিল আইয়ুব খানের, তখন সেই সমারোহ যেমন করে বিদ্বিষ্ট করে তুলছিল পাঠকদের (যার খবর প্রচারকরা রাখত না), তেমনিভাবে প্রলুব্ধ ও স্তাবক বুদ্ধিজীবীদের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার বর্ধিষ্ণু সমারোহও ঘৃণার সৃষ্টি করেছিল মানুষের মনে। বিশেষ করে আইয়ুবের রাজত্বকালে, কেননা সেই কালেই উদ্যোগ-আয়োজনটা বেড়েছিল সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশ মীরজাফরদের জন্ম যেমন দিয়েছে, তেমনি তাদের ঘৃণা করতেও কার্পণ্য করেনি।
বুদ্ধিজীবীদের যে অংশ জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরকারের তাঁবেদার হিসেবে কাজ করেছে, তাদের প্রতি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা মানুষকে বিক্ষুব্ধ করেছে। ১৯৬৮ সালে অগ্রগতির ১০ বছরের গুণকীর্তন করে যখন প্রায় প্রতিদিন সংবাদপত্রে একটি করে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছিল, যখন প্রতিদিন মস্ত মস্ত ছবি ছাপা হচ্ছিল আইয়ুব খানের, তখন সেই সমারোহ যেমন করে বিদ্বিষ্ট করে তুলছিল পাঠকদের (যার খবর প্রচারকরা রাখত না), তেমনিভাবে প্রলুব্ধ ও স্তাবক বুদ্ধিজীবীদের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার বর্ধিষ্ণু সমারোহও ঘৃণার সৃষ্টি করেছিল মানুষের মনে। বিশেষ করে আইয়ুবের রাজত্বকালে, কেননা সেই কালেই উদ্যোগ-আয়োজনটা বেড়েছিল সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশ মীরজাফরদের জন্ম যেমন দিয়েছে, তেমনি তাদের ঘৃণা করতেও কার্পণ্য করেনি।
বুদ্ধিজীবী সমাজের যে অংশ সাধারণ মানুষের সঙ্গে ছিল, তারা বিবেকবান ছিল সত্য; কিন্তু তারাও আসলে নিজেদের স্বার্থেই কাজ করেছে, তবে তফাত এই যে তাদের স্বার্থকে তারা জনসাধারণের স্বার্থ থেকে ভিন্ন করে দেখেনি। এবং উভয়ের স্বার্থ যেহেতু ছিল এক ও অভিন্ন, তাই তাদের কাজের ফলে জনসাধারণের আন্দোলনের উপকার হয়েছে।
পাকিস্তান আন্দোলনের পেছনে কোনো দার্শনিক প্রস্তুতি ছিল না; যদিও পরবর্তীকালে প্রচার করা হয়েছিল যে বিশিষ্ট জীবনদর্শনের প্রয়োজনেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের আন্দোলনও কোনো গ্রন্থপাঠ থেকে শুরু হয়নি। কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা এই আন্দোলনে ছিলেন, এই আন্দোলনে তাঁরা সরাসরি নেতৃত্ব দেননি, আন্দোলন যখন এগিয়ে গেছে তখন তার গতির সঙ্গে সমতা রক্ষা করতেও হয়তো তাঁরা পারেননি, পিছিয়ে পড়েছেন, তবু তাঁরা সঙ্গেই ছিলেন, তাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ভূমিকাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সভা করে গুলিবর্ষণের নিন্দা করেছেন, ফলে তাঁদের ভেতর থেকে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। উনসত্তর ও একাত্তরের আন্দোলনের সময় শিক্ষকরা রাজপথে শোভাযাত্রা করেছেন।
এসব ঘটনা ছোট ঘটনা। কিন্তু এগুলোর তাৎপর্য আছে। তাৎপর্য এই যে বোঝা গেছে বিক্ষোভ সর্বজনীন হয়ে উঠেছে, তার চেয়ে বড় কথা বোঝা গেছে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব মানুষ এক হয়ে গেছে। সেই একতার দরুনই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।
বুদ্ধিজীবীদের প্রলোভন দেখানোর কাজ পাকিস্তান সরকার শুরু থেকেই করেছে। উদ্দেশ্যটা সহজ। সরকার চেয়েছে জনসাধারণকে শোষণ করতে বুদ্ধিজীবীরা যদি জনসাধারণের অংশ হয়ে যায়, জনসাধারণের সঙ্গে থাকে, তবে তারা মানুষের চোখ খুলে দিতে পারে, চোখ খুলে দিলে শোষণ করতে অসুবিধা। আর যদি বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে পাকিস্তানের মহিমা প্রচার করানো যায়, তাহলে শোষণ কাজটা আরো নির্বিঘ্নে হতে পারে। বুদ্ধিজীবীদের জীবনে যেহেতু অভাব ছিল সচ্ছলতার এবং লোভ ছিল স্বাচ্ছন্দ্যের, তাই অল্পতেই তাঁরা আকৃষ্ট হতেন। চাকরিতে উন্নতি, পুস্তকের জন্য পারিশ্রমিক পরবর্তীকালে তমঘা ও পুরস্কার, বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ এসবের সাহায্যে জনসাধারণ থেকে বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস সরকার করেছে, সক্ষমও হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। বুদ্ধিজীবী সমাজের, লেখক, শিক্ষক, সাংবাদিক, ব্যবহারজীবী তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট যাঁরা, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তাঁদের প্রায় সবার জীবনেই সমৃদ্ধি এসেছে। তাই পাকিস্তানের প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতাবোধ না থেকে পারেনি, তাঁদের জীবন ও সাধারণ মানুষের জীবন বিপরীত দিকে চলেছে, অনিবার্যভাবেই। তুলনায় যাঁরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন কম তাঁদের পক্ষেও সরকারি বক্তব্য সমর্থন না করে উপায় থাকেনি। এর কারণ তাঁদের জীবনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাবোধের অভাবটা ছিল আরো বেশি, তাঁরা ভয় পেয়েছেন যে সামান্য ধাক্কায়ই তাঁরা গড়িয়ে পড়বেন নিচের খাদে। এবং ধাক্কার আশঙ্কা সব সময়ই ছিল—সরকার শুধু প্রলোভনই দেখায়নি, ভয়ও দেখিয়েছে। এবং প্রলোভনের তুলনায় ভয় কিছু কম শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেনি। ভয়ের জন্য ভুলকে ভুল, অন্যায়কে অন্যায় বলে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। মধ্যবিত্তের মনেও অর্থনৈতিক অসন্তোষ ছিল; কিন্তু সেই অসন্তোষ কিংবা তার চেয়েও বড় অসন্তোষ সাধারণ মানুষের অসন্তোষকে উন্মোচিত করার মতো পর্যাপ্ত সাহস বুদ্ধিজীবীদের অনেকের মধ্যেই দেখা যায়নি। ভয়টা কল্পিত ভয় ছিল না। বামপন্থী বলে পরিচিত যাঁরা, প্রয়োজনবোধে তাঁদের কারাগারে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে সরকার দ্বিধা করেনি। অন্যদিকে অবাধে চিন্তা ও মতামত প্রকাশ করার সুযোগ বা স্বাধীনতা কোনো দিনই ছিল না বাংলাদেশে। যেমন—পত্রপত্রিকা প্রকাশের কথা উল্লেখ করা যায়। এমনিতে এই কাজটা দুরূহ ছিল অর্থনৈতিক কারণে। তদুপরি পত্রিকা প্রকাশ করতে হলে আগে অনুমতি নিতে হতো সরকারের। সরকারের অপছন্দ হলে চালু পত্রিকা যেকোনো সময় বন্ধ করা হতো। সম্পাদককে কারাদণ্ডাদেশ দেওয়ার উদাহরণও অজানা নয়।
জনতার সঙ্গে চলা বুদ্ধিজীবী সমাজ জনতার অগ্রবর্তী অংশ হিসেবেই কাজ করেছে। পাকিস্তানের ব্যর্থতার লক্ষণ প্রথম ধরা পড়েছে তাঁদের কাছেই, পরে তাঁরাই প্রমাণ পেয়েছেন সেই ব্যর্থতার। তাঁরাই বুঝেছেন ভাষার ওপর আক্রমণের অর্থ কী, অর্থনীতির গতি কোন দিকে। সেই জ্ঞানকে তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। বাকি কাজটা সাধারণ মানুষ নিজেরাই করেছে। বাংলাদেশকে তারা স্বাধীন করে নিয়েছে নিজের হাতে।
লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
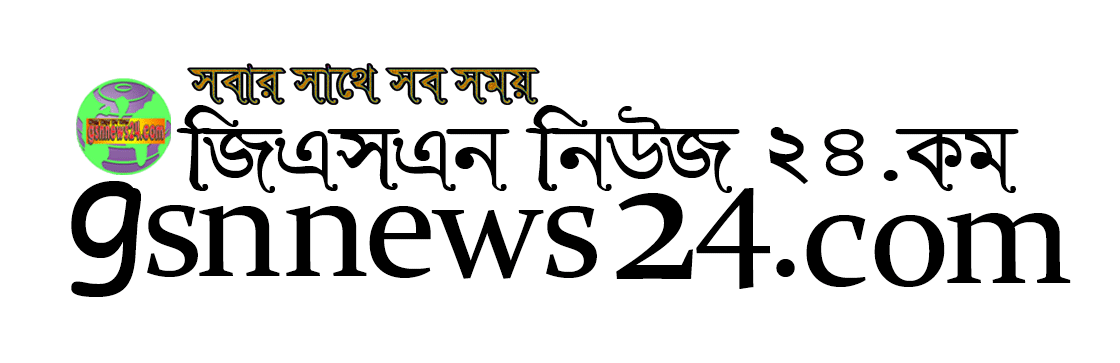
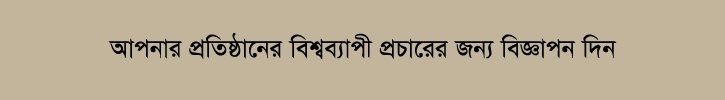

























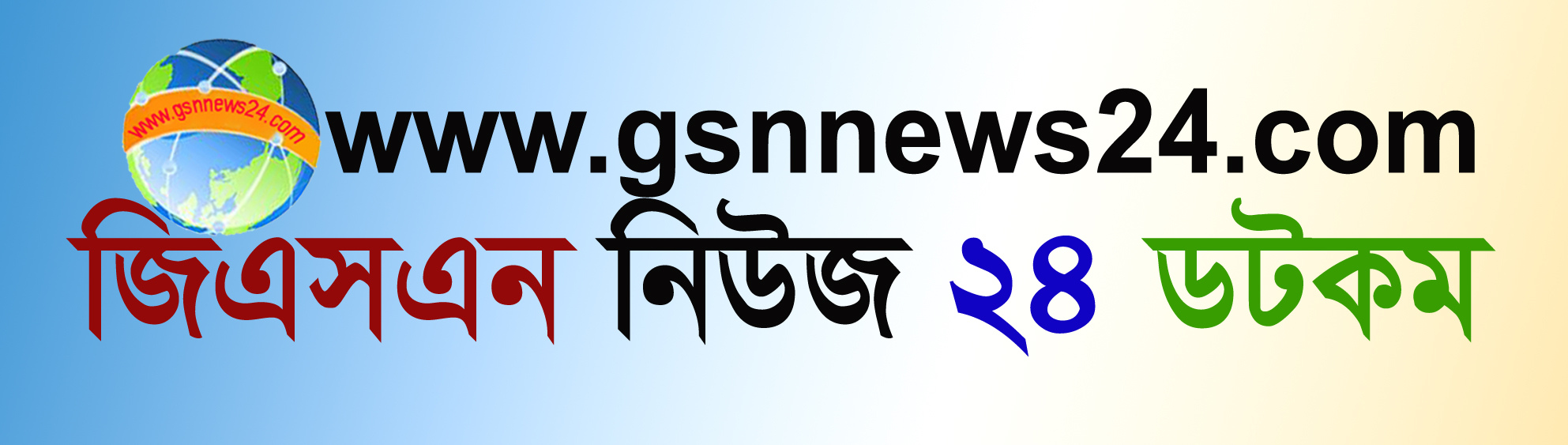
Leave a Reply